পিএইচডি, উচ্চপদস্থ এই ডিগ্রীর পূর্ণরূপ হল ডক্টর অফ ফিলোসোফি। কোথাও আবার এটাকে ডি ফিল ও বলা হয়। সাধারনত মাস্টার্স পাশ করার পর একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণার পাশাপাশি আরও কিছু বিশেষায়িত ও উচ্চতর কোর্স ওয়ার্ক করানো হয় (মূলত উত্তর আমেরিকায়; জাপান, কোরিয়া, চীন, যুক্তরাজ্যে কোর্স ওয়ার্ক নেই)। এই ডিগ্রী কারা করেন? বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের গণহারে পিএইচডি থাকা বাঞ্ছনীয়, আর পদোন্নতি ও এর সাথে সম্পর্কিত। কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে তবে সেগুলোতে পিএইচডি এর কোন বাধ্যবাধকতা নেই, এছাড়াও অনেক এনজিও এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা ফেলোগণ ও এটি করে থাকেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক গবেষণার প্রয়োজনে। যেহেতু পিএইচডি হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে পঠিত, গবেষণালব্ধ ও মাঠ জরিপকৃত ফলাফলের এক বিশাল সমাহার তাই এই সুবিশাল জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ঐ বিষয়ের অনাবিষ্কৃত কোন অংশে দার্শনিক ভাবনার মাধ্যমে একধাপ এগিয়ে যাবার কারনেই এর নামের শেষে ফিলোসোফি যুক্ত হয়েছে।
এই ডিগ্রীর উদ্দেশ্য আসলে কি? পিএইচডি এর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হল নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি ও এর মাধ্যমে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ অব্যাহত রাখা। যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান দুটি কাজ হচ্ছে জ্ঞান বিতরণ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা তাই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য এটি অনেকটাই অপরিহার্য একটি ডিগ্রী। সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনী গবেষণার হাতে খড়ি হয়ে থাকে এখানেই এবং কেউ এটি সম্পূর্ণ করতে পারলে ধরে নেওয়া হয় তিনি পরবর্তীতে এই বিষয়ে তার দর্শনকে কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন আবিস্কার করতে সক্ষম।
একাডেমিক দিক থেকে পিএইচডি টার্মিনাল ডিগ্রী হলেও গবেষণায় এটি কেবলই প্রবেশদ্বার মাত্র সে কারনেই উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকতার ন্যূনতম যোগ্যতা হল এই পিএইচডি। আমেরিকা আরও একধাপ এগিয়ে, সেখানে প্রয়োজন পিএইচডি সহ ১-২ বছরের পোষ্টডক্ গবেষণার অভিজ্ঞতা; ওরা এটি নিশ্চিত করে যে যাকে শিক্ষক কাম গবেষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হবে তার চিন্তা করার ক্ষমতা তথা ফিলোসোফি অনেক হাই। এরপর তাদের চাকুরী স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির সকল পর্যায়ে দেখা হয় তার কতটি প্রকাশনা আছে, সেগুলো কেমন মানের জার্নালে, কতজন শিক্ষার্থীকে পিএইচডি সুপারভিশন করেছেন ইত্যাদি; এতকিছুর পরে তিনি হয়তো অধ্যাপক।
এবার বাংলাদেশে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে এখানে মাস্টার্স ডিগ্রীধারীদের প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর পদোন্নতির মাধ্যমে ২-৩ বছরের মধ্যেই সহকারী অধ্যাপক, তারপর শিক্ষাছুটি এবং যেনতেনভাবে (সবাই নয় তবে অধিকাংশ) পিএইচডি অর্জন। কেউকেউ তো সহযোগী অধ্যাপক এমনকি অধ্যাপক হওয়ার পরে পিএইচডি করতে সীমান্ত পাড়ি দেন। অনেকের তো আবার পিএইচডির বিষয় আর নিয়োগকৃত বিষয়ের মধ্যে কোন মিল নেই, শুধুই মুখ রক্ষার ডক্টর। এইদেশে শিক্ষকদের অবস্থা যতটা না দৈন্য, রাষ্ট্র তার থেকেও বহুগুন বেশি দৈন্য। বালিশ/ পর্দা কাণ্ড, খিচুরি রান্না বা সাঁতার শেখার জন্য বিদেশ সফর, করোনার টাকায় কানাডায় ছেলেকে ব্যবসা খুলে দেওয়া, রাষ্ট্রীয় খরচে প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সফর এসব কিছুর জন্য টাকার অভাব না হলেও মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা, নিরাপদ স্বাস্থ্য সেবা বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ন্যূনতম চলনসই ল্যাব নির্মাণের টাকা এদেশের জনগন যোগাতে পারেনা।
যাইহোক, ডিগ্রী শেষে ফিরে সহযোগী অধ্যাপক, আরও ৩-৪ বছর পর অধ্যাপক। এভাবে পিএইচডি ও কিছু যেনতেন মানের প্রকাশনা দিয়ে অধ্যাপক হওয়ার পর তিনি হলেন সিনিয়র শিক্ষক; গবেষণার তো বালাই নাই উপরন্তু মর্জি অনুযায়ী ক্লাস নেওয়া যার ৭০-৮০ ভাগই হল প্রস্তুতি বিহীন স্লাইড শো। সাথে আছে রাজনীতি, ১২ মাসে ১৩ ক্যাম্পাস নির্বাচন, ভিসির পক্ষে-বিপক্ষে আন্দোলন ও মানব বন্ধন ইত্ত্যকার বিষয়াদি।
এবার আসা যাক যে শিক্ষক/ গবেষক খুবই নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সাথে টপ র্যাঙ্কড কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি- পোষ্টডক্ সম্পন্ন করে দেশে ফিরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত/ পুনঃনিয়োজিত হন দেশীয় শিক্ষায় তিনি কতটুকু অবদান রাখতে পারেন? বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা মোস্টলি তত্ত্বীয়, গবেষণার অংশ এখানে খুবই সীমিত। মাস্টার্স পর্যায়ে অতি নিম্নমানের থিসিস এবং হাতে গোনা গুটিকয়েক বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক শেষ পর্বে সংক্ষিপ্ত প্রজেক্ট করানো হয়। ক্লাসে যেহেতু ছকে বাঁধা সিলেবাস পরানো হয় তাই একজন শিক্ষক তার পিএইচডি ও পোষ্টডক্ জীবনে যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেন সেসবের ন্যূনতম অবতারণা করাও সম্ভব হয় না শিক্ষার্থীদের মাঝে। নিম্ন মানের থিসিস বলাতে হয়তো অনেকে মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন, তাহলে এবার এটিও ব্যাখ্যা করা যাক। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রায় সবাই স্নাতক সম্পন্ন করেই চাকরিতে ঢুকে পরে বা বিদেশে পাড়ি জমায়। মাস্টার্স করার রীতি বা প্রয়োজন এখানে চোখে মেলেনা (১-২ জন ছাড়া যারা শিক্ষকতায় যোগ দেয়)।
অন্যদিকে জেনারেল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ৪র্থ বর্ষে ওঠার সাথে সাথেই খোজ শুরু করে দেয় যে আসন্ন বিসিএস এ তারা অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা; একাডেমিক লেখাপড়া সাইডে রেখে মোটামুটি ৮০ ভাগ শিক্ষার্থীই ক্লাসে বসে প্রফেসরস বা এমপিথ্রি সিরিজের বই নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ক্লাস শিক্ষকও বাস্তব সম্মত কারনেই সেদিকে খুব বেশি দৃষ্টিপাত না করে তাঁর দায় সেরে ক্লাস থেকে বেড়িয়ে পরেন কারন তিনি খুব ভাল করেই জানেন যে তাঁর এই একাডেমিক জ্ঞান গর্ভ আলোচনা শিক্ষার্থীদের রুটি রুজির জন্য মোটেও সহায়ক নয় বরং সিজিপিএ ২.৫ পেয়েও তাঁর শিক্ষার্থীরা নামজাদা কর্মকর্তা হয়ে রীতিমত মোটিভেশনাল স্পিকার বনে যেতে পারে। ৪র্থ বর্ষের ঝিকঝিক করে চলতে শুরু করা ট্রেন মাস্টার্সে এসে তো ফুল বুলেট ট্রেনের রুপ নেয়। শিক্ষার্থীরা এই প্রফেসরস বা এমপিথ্রি বই হাতে নিয়ে গবেষণায় কতটুকু নিমজ্জিত হতে পারে বলে আপনি মনে করেন, তা সংশ্লিষ্ট গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক যত পণ্ডিত ব্যক্তিই হোন না কেন? আর দেশে পিএইচডি এর কথা তো বলাই বাহুল্য। নিজের গবেষণার টাইটেল টাও ডিফেন্স এর সময় ইংরেজিতে বলতে পারে না; কাট- কপি- পেস্ট করে থিসিস বুক কোনরকমে জমা দিলেও প্রকাশনার কোন তলা খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে শিক্ষকদের কষ্টার্জিত এই পিএইচডি ও পোষ্টডক্ এর আউটপুট কতটা? উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের আলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমার দৃষ্টিতে পিএইচডি একটা অরনামেন্টাল ডিগ্রী ছাড়া বিশেষ কিছু নয় (৫% ব্যতিক্রম হতে পারে)।
উচ্চশিক্ষা, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা, পিএইচডি, পোষ্টডক্ এসব কিছুই উন্নত বিশ্বের ভাবনা প্রসূত। তারা তাদের আর্থ, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় তাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছে। কথায় আছে অনুসরন মানুষের কাজ আজ অনুকরণ বানরের। আশ্চর্যজনক ভাবে আমরা যুগের পর যুগ অন্ধভাবে পশ্চিমা বিশ্বকে বানরের মত অনুকরণ করেই চলছি আমাদের পরিস্থিতি ও বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। যেখানে খুব সাধারন একটা সর্দি-জ্বরের ওষুধের কার্যকারিতা দুটি ভিন্ন অঞ্চলে পুরোপুরি ভিন্ন হতে পারে সেখানে বিদেশি রাষ্ট্রের পলিসির হুবহু নকল করে কি অর্জন করা সম্ভব? রাশিয়া, চীন, আমেরিকা তিনটি রাষ্ট্রই পরাশক্তি কিন্তু তাদের পলিসি ও ওয়ে অফ অ্যাক্টিং সম্পূর্ণ আলাদা; কেউ কাউকে কপি করে পরাশক্তি হয়নি আর সেটা সম্ভব ও না। যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেই যে শুধুমাত্র অর্থের অভাবে আমরা উচ্চশিক্ষায় গবেষণাকে সেভাবে সযুক্ত করতে পারিনি, তাহলে আমাদের প্রয়োজন ও বাস্তবতার আলোকে কেন ভিন্ন কোন কার্যকরী উপায় খুঁজে বের করিনি?
যেহেতু আমাদের শিক্ষা প্রায় পুরোটায় তত্ত্বীয় ধাচের তাই আমরা পিএইচডি এর বিকল্প হিসেবে সমমানের কোন তত্ত্বীয় ডিগ্রী চালু করতে পারতাম; তখন একজন শিক্ষক তাঁর পছন্দের বিষয়ে আরও ২-৩ বছর তত্ত্বীয় পড়ালেখা করে গবেষণা পিএইচডি এর পরিবর্তে তত্ত্বীয় পিএইচডি বা ডি ফিল (থিউরি) অর্জন করে শ্রেণীকক্ষে তাঁর এই অর্জিত জ্ঞান সহজেই শিক্ষার্থীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ও প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখতে পারতেন আর এখানে টিচিং প্রফেসর কনসেপ্ট টা আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হত। অনেকে ভাবছেন যে থিউরি পিএইচডি এ আবার কেমন জিনিস, এই প্রথম শুনলাম। আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমরা সেভাবে চিন্তা করতে শিখিনি, আউট অফ দ্য বক্স ভাবতে পাড়াটা যেকোনো জাতির জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ, কারন এই ভাবনাই তাকে সকল সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি দিতে পারে।
এই ধরুন যে বাংলাদেশে ৫০ কিমি রাস্তা ৪ লেনে উন্নিত করার জন্য বিশ্ব ব্যাংক, জাইকা, আইএমএফ, চীন এমনকি ভারতের কাছেও উচ্চ সুদে ঋণ ভিক্ষা করে সেখানে আমেরিকা কিভাবে ৮-১০ লেনের হাজার হাজার কিমি রাস্তা বানিয়েছে বহুবছর আগেই, কারো কাছে ভিক্ষা করেনি বরং ভিক্ষা দিয়েছে আর আজও তা দিয়েই যাচ্ছে। পলিসি কি? মাথা খাটিয়েছে, কূটনীতি দিয়ে যুদ্ধ বাধিয়েছে, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলারের অস্ত্র ব্যবসা করেছে, আবার সেই অর্থেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল ও গরীব দেশে সহযোগিতা করে বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। চীনের সস্তা উৎপাদন নীতি, জাপানের ট্রাস্ট ইজ ভ্যলু ও মডেস্টি নীতি, মালয়েশিয়ায় এন্টি করাপশন নীতিই হল তাদের উন্নত হওয়ার রহস্য; তারা কেউ কাউকে অনুকরণ করেনি, যা করেছে তা হল এক্সপানসন অফ থিঙ্কিং। আমেরিকায় পিএইচডি প্রোগ্রামে কোর্স ওয়ার্ক বাধ্যতামূলক, জাপানে নয়; ওরা শুধু গবেষণা করেই পিএইচডি দেয়। ওরা কোর্স ওয়ার্ক এডোপ্ট করেনি তবুও ওদের শিক্ষার মানে ভাটা পরেনি, বরং প্রতি বছর নোবেল লরিয়েটদের মধ্যে জাপানের কেউ না কেউ থাকেই। তাহলে এখন বলুন থিউরি পিএইচডি কি কোন আজগুবি তত্ত্ব নাকি আমাদের জন্য এটাই সবথেকে প্রডাক্টিভ হতে পারতো?
আগেই যেহেতু বলছি যে পিএইচডি আমার মতে একটি অলংকারিক ডিগ্রী, তো এবার দেখা যাক যে এই ডিগ্রী যিনি অর্জন করেন তাঁর জীবন কতটা অলংকৃত হয়। সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি নিয়েই অধিকাংশ শিক্ষক পিএইচডি করতে চলে যান। ৩-৫ বছর পর ফিরে এসে যা পান তা হল তিনটি বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যা শুধু চলতি পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; পরবর্তী পদে পদোন্নতি পেলে সেটি বন্ধ হয়ে যায় (মাস ছয়েকের মধ্যেই প্রায় সবাই সহযোগী অধ্যাপক হয়ে যান)। যদিও এটি কতবার রহিত আবার সচল করা হয়েছে তার হিসেব নেই। অবশেষে ইউজিসি তো সাফ চিঠি দিয়ে কড়া ভাবে জানিয়ে দিল যে এই ইনক্রিমেন্ট নাকি শুধু ক্যাডার সার্ভিসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, বিশ্ববিদ্যালয়কে এটি দেওয়া বন্ধ করতে
হবে (এখন যদিও সেটি আবার চালু হয়েছে)। আমার বুঝে আসেনা যে গাধাগুলোকে বেছে বেছে চেয়ারে বসানো হয় নাকি চেয়ারে বসার পর ওনারা মাননীয় গাধা হয়ে যায়? যাইহোক আলোচনায় ফিরি, পিএইচডির পর ঐ শিক্ষক যা পান তা হল নামের পূর্বে ডঃ, আর কয়েকমাস বিশেষ ইনক্রিমেন্ট যা মাসে ১০,০০০ টাকার বেশি নয়।
যিনি পিএইচডির পর সরাসরি সহকারী অধ্যাপক পদে (৬ষ্ঠ গ্রেড) যোগ দেন (প্রস্তাবিত অভিন্ন নিতিমালায় এটিকে বাদ দিয়ে প্রভাষক পদে যোগদান করানোর কথা বলা হয়েছে, অথচ সারা বিশ্বেই পিএইচডির পর সরাসরি সহকারী অধ্যাপক পদে যোগ দেওয়ার নিয়ম) তার মূল বেতন হয় ৩৫,৫০০ টাকা।
৯ম গ্রেড থেকে চাকুরির মাধ্যমে ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতি পেতে সময় লাগে ক্ষেত্র বিশেষে ৩-৫ বছর।
আপনার কোন এক বন্ধু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাশ করে ৩-৫ বছর ৯ম গ্রেডে চাকরি করে ৬ষ্ঠ গ্রেডে গেল আর আপনি অনেক অনেক ভাল ফলাফল সহ মাস্টার্স পাশ করে, জিআরই, টোফেল, আইএলটিএস করে বিদেশে ৩-৫ বছর পিএইচডি করে দেশে ফিরে মফস্বলে মাস্টারির চাকরি নিলেন ৩৫,৫০০ টাকা মূল বেতনে।
জীবন যুদ্ধে কে এগিয়ে গেল বলেন তো? বিদেশের চোখ ধাঁধানো জীবনের হাতছানি ছেড়ে একজন ডক্টর যখন মফস্বলের বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তখন সেখানে কতটুকু নাগরিক সুবিধা তিনি পান? না আছে ভাল কোন বিনোদন কেন্দ্র বা শপিংমল, না আছে ছেলেমেয়েকে পড়ানোর জন্য ভাল স্কুল-কলেজ, না আছে কোন সামাজিক প্রটোকল! আর কেউ যদি দেশে না ফেরেন তবে বছরে একবার জাতীয় দৈনিকের প্রথম পাতায় শুধুই একটা প্রতিবেদন ছাপা হয় ব্রেইন ড্রেন বা মেধা পাচার শিরোনামে!

লেখকঃ মেজবাহ হোসেন,
প্রভাষক, হাবিপ্রবি (বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত)
Mezbahhossain15@gmail.com
ইবাংলা/আরএস/১০ অক্টোবর,২০২২
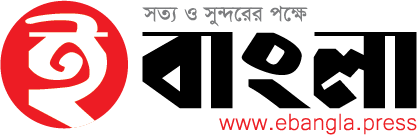
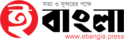



মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়েছে.